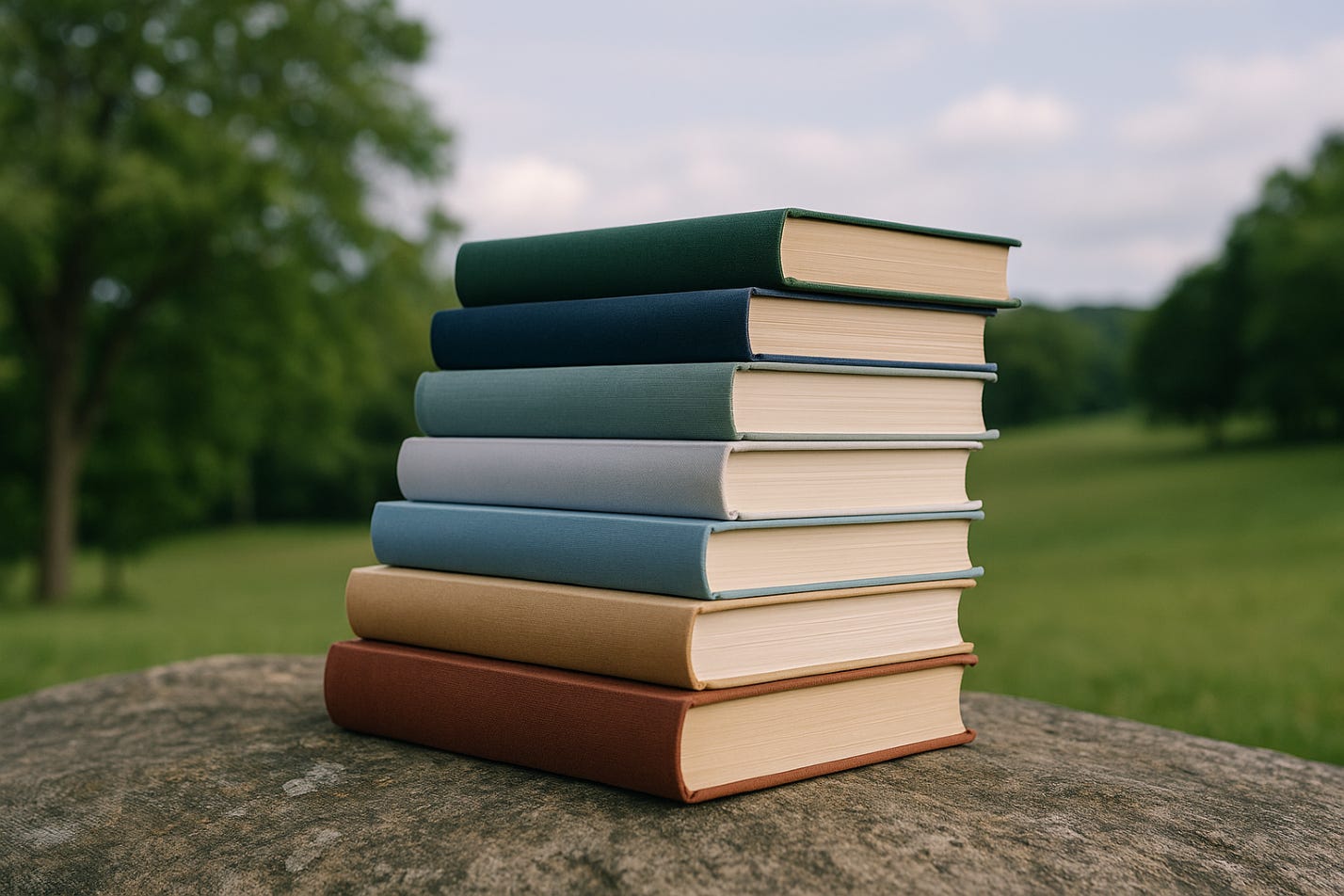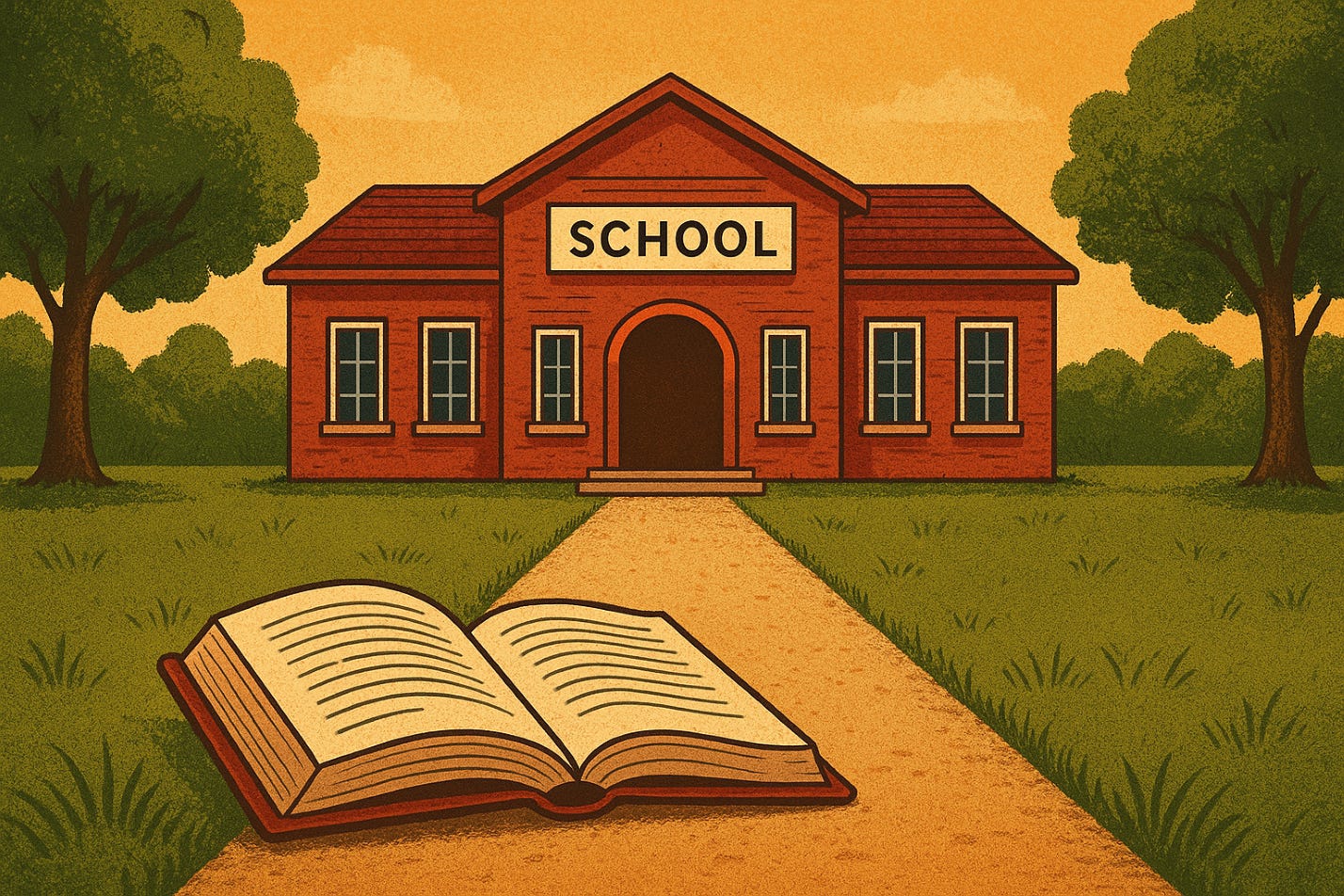আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাঃ কোথায় দাঁড়িয়ে, কি করণীয় (পর্ব ২ )
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট অনুধাবনে প্রয়োজন কমিশনের সুপারিশ, রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ। টেকসই উন্নয়নে দরকার ঐকমত্যভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষানীতি।
The education system in Bangladesh faces persistent challenges, including policy inconsistency, political interference, weak funding, and poor teacher training. Despite ambitious commissions and reforms, real progress remains stalled. Sustainable change demands a long-term, consensus-driven education policy, adequate funding, and depoliticized institutions to ensure inclusive, modern, and future-ready education for all citizens.
শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রথম পর্বের আলোচনায় মূল ফোকাস ছিল বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা, সরকারের ভূমিকা এবং অত্যাধুনিক ও টেকসই উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ। আলোচনাটি এই লিংকে পড়া যাবে: (https://theinsighta.com/p/50f)। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় শিক্ষানীতির অসঙ্গতি, পাঠ্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত উদ্যোগের অভাবের দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝার জন্য নিম্নোক্ত ৪টি বিষয় জানা প্রয়োজন:
১। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও কারিকুলাম পর্যালোচনা
২। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
৩। অর্থনৈতিক বাস্তবতা
৪। সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
১) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও কারিকুলাম পর্যালোচনা
প্রতিটি কমিশন যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নানা সুপারিশ প্রদান করেছে। তবে জাহান ও চৌধুরী তাদের ২০১৪ সালের Education and political culture in Bangladesh গবেষণায় বলেছেন, বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি।
শিক্ষাখাতের বিবর্তন, সমস্যা ও উন্নয়ন বুঝতে হলে আমাদের বিগত শিক্ষা কমিশনগুলোর সুপারিশগুলো জানতে হবে। তবে এই লেখায় সব কটি কমিশনের সুপারিশ আলোচনা না করে শুধুমাত্র এই শতাব্দীতে, অর্থাৎ গত ২৫ বছরে যে ২টা প্রধান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং শিক্ষা নীতিমালা তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, কারন এই সুপারিশগুলো বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।
মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন (২০০৩)
মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়– সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, এবং বিশেষায়িত শিক্ষা।
এই রিপোর্টে মোট ৮৮০টি সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- শিক্ষায় সমান সুযোগ- ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার পার্থক্য নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল, সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের প্রস্তাব, একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস ও শিক্ষকদের যোগ্যতা উন্নয়ন, কারিকুলাম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কার, মাধ্যমিক স্তরে মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জীবিকা অর্জনের সুযোগমুখী শিক্ষা প্রদান।
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ হবে স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে এবং শিক্ষকদের বেতন স্কে ল, পদোন্নতি ও চাকরির শর্ত এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
উচ্চশিক্ষার ব্যপারে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরুৎসাহিত করে বলা হয়–- কৃষি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি অর্থে একমুখী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, তবে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ প্রতিষ্ঠা।
এর বাইরে উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হল- দেশে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব, শিক্ষা প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ, একটি জাতীয় বিজ্ঞাননীতি তৈরি ও দ্রুত বাস্তবায়ন, একটি জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন।
তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলো জাতীয় শিক্ষানীতিতে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়নি।
কবির চৌধুরী শিক্ষা কমিশন (২০০৯)
কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে ২০০৯ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ-এর আলোকে সরকার ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। এটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বিস্তৃত শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা।
শিক্ষার কাঠামো নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। এর ফলে প্রাথমিক স্তরের মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করা হয়। মাধ্যমিক স্তরকে চার বছর মেয়াদি করা হয় (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)। অর্থাৎ স্নাতকপূর্ব শিক্ষাকে প্রচলিত তিন ধাপ থেকে দুই ধাপে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়।
মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে পরীক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়। অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু করার কথা বলা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে দশম শ্রেণি শেষে সরকারি বৃত্তি পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণি শেষে মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।
২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানমুখী করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের সব প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। এর মাধ্যমে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরাও কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষিত বেকারত্ব কমবে।
মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করা হয়। একইসাথে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করে আধুনিক বিজ্ঞান ও সামাজিক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।
শিক্ষকদের মানোন্নয়নকে অন্যতম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য একটি আলাদা শিক্ষক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়, যা নিয়োগ, বেতনভাতা, পদোন্নতি ও চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করবে। শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মূলত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত, সময়োপযোগী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কর্মসংস্থানমুখী করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, মাধ্যমিক কাঠামোর সংস্কার, আবশ্যিক বিষয় সংযোজন, মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষক উন্নয়ন এবং একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের মতো যুগান্তকারী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তবে নীতি বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কারিকুলাম পর্যালোচনা ও সংস্কার
শিক্ষানীতি ২০১০ (জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০১০-এর ভিত্তিতে)
বাংলাদেশে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন মূলত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের কারিকুলাম সংস্কার এবং ২০২১–২০২৫ সালের নতুন কারিকুলাম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
২০১২ সংস্কার: সৃজনশীল পদ্ধতি (creative question system) চালু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মুখস্থ-নির্ভরতা কমিয়ে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক চিন্তন বাড়ানো। কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাবে এটি পরীক্ষাভিত্তিক চাপ বৃদ্ধি করেছে।
ধাপে ধাপে পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা থেকে outcome-based education (OBE)-এ রূপান্তর।
ক্লাস ৯-১০-এ বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য বিভাজন বাতিল।
ক্রমাগত মূল্যায়ন (continuous assessment) চালু।
শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, জীবন দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে জোর।
প্রধান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা
নীতির ধারাবাহিকতার অভাব: প্রতিটি সরকার নতুন কমিশন গঠন করলেও পূর্ববর্তী নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।
অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা: শিক্ষা বাজেট GDP-র মাত্র ২%–এর সামান্য বেশি, যা আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অপ্রতুল।
শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি: নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে যোগ্য শিক্ষক তৈরির অভাব বড় বাধা।
রাজনৈতিক প্রভাব: পাঠ্যবইয়ে মতাদর্শিক প্রভাব ও ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ বারবার উঠেছে।
পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা: সংস্কারের পরও মুখস্থ-নির্ভরতা কমেনি, বরং পরীক্ষার চাপ বেড়েছে।
বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনগুলোর সুপারিশ যুগোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবায়নের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। সাম্প্রতিক কারিকুলাম সংস্কার শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পর্যাপ্ত বাজেট, এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর। যেটা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে একটি জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি এবং ধারাবাহিক কারিকুলাম উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষাখাতকে টেকসই উন্নয়নের পথে নেওয়া সম্ভব নয়।
২) রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি অস্থিতিশীলতার কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস হিসেবে কাজ করে, যেখানে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের মতাদর্শ প্রজন্মের মধ্যে প্রোথিত করতে সচেষ্ট থাকে। ফলস্বরূপ শিক্ষানীতি বারবার রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবর্তিত হয় এবং শিক্ষার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
Kochanek তার ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Patron-Client Politics and Business in Bangladesh বইয়ে বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঐতিহাসিকভাবে দলীয় বিভাজন, ক্ষমতাকেন্দ্রিকতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা-ভিত্তিক রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সংস্কৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে শিক্ষা মূলত জাতি গঠনের পরিবর্তে রাজনৈতিক আনুগত্য গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক প্রভাব
নীতির অস্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার অভাব: হামিদ রহমান এবং খান ২০১৯ সালের তাদের Education Policy in Bangladesh: Continuity and Change আর্টিকেলে দেখিয়েছেন, একেক সরকার ক্ষমতায় এসে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৭৪, ১৯৮৮ ও ২০১০ সালের শিক্ষানীতি একে অপরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, ফলে দীর্ঘমেয়াদে কোনো পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি।
প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ: বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের প্রশাসনিক নিয়োগে রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এটি Weber-এর meritocracy model-এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার কথা।
ছাত্ররাজনীতি ও সহিংসতা: শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক সহিংসতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শিক্ষা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্র, কিন্তু বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি প্রায়শই দলীয় সংঘাত, টেন্ডারবাজি ও সহিংসতায় রূপ নেয়।
পাঠ্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: এইচ কবির তার ২০২০ সালের Political Influence in Curriculum Development in Bangladesh গবেষণায় দেখিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি বা মতাদর্শভিত্তিক বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। Althusser-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, এটি শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শ প্রজন্মের মধ্যে প্রোথিত করার কৌশল।
অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা: UNESCO-এর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০% বরাদ্দ দেওয়ার কথা, কিন্তু বাংলাদেশে তা প্রায়শই ১২–১৪%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উপেক্ষিত থাকে।
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রভাব ও দলীয় সংস্কৃতির কারণে তার মূল যে উদ্দেশ্য– যোগ্য, নৈতিক ও সৃজনশীল নাগরিক গঠন– তা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এসব নেতিবাচক প্রভাবের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের অবনতি, শিক্ষক ও প্রশাসনের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি, ছাত্রসমাজের মধ্যে সহিংসতা ও দলীয় দাসত্বের প্রবণতা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ব্যর্থতা, সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও সুশাসনে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, শিক্ষার কাংখিত ফলাফল থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয়।
এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন একটি জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি, যা সরকার পরিবর্তন হলেও অপরিবর্তিত থাকবে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে, বাজেট বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং গবেষণা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাখাতকে জাতীয় উন্নয়নের প্রকৃত চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।
৩) অর্থনৈতিক বাস্তবতা
World Bank এর ২০২০ সালের তথ্য মতে, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে সাক্ষরতার হার ও শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও গুণগত মান, অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও গবেষণায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাখাতে ধারাবাহিক ও যথাযথ অর্থায়ন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল কার্যকর করা সম্ভব নয়।
শিক্ষাখাতে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের বর্তমান অবস্থা
GDP অনুপাতে বরাদ্দ: বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে বার্ষিক বাজেট GDP-র মাত্র ২–২.৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এটি ৪–৬% হওয়া প্রয়োজন।
জাতীয় বাজেট অনুপাতে বরাদ্দ: জাতীয় বাজেটের প্রায় ১১–১৩% শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায়ও কম।
তুলনামূলক পরিসংখানে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বার্ষিক ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। GDP এবং জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের দিকে তাকালে ফারাকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
GDP-এর অনুপাতে শিক্ষা ব্যয়
দেশ
শিক্ষা বাজেট (% of GDP)
বাংলাদেশ
বিশ্ব গড়
4.4-4.5%
আর্থ-উচ্চ আয়ের OECD দেশসমূহ
গড়ে 5.1%
নিম্ন আয় গ্রুপ দেশসমূহ
~3.6-৪.০%
উচ্চ ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহ
এই পরিসংখানগুলো থেকে স্পষ্ট যে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বাজেটের অংশ বিশ্বগড় বা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ, OECD দেশগুলোর গড় প্রায় ৫.১% কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র ১.৭-১.৮%, যা আধুনিক দেশগুলোর তুলনায় প্রায় অর্ধেক বা তারও কম। নিম্নআয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রে LICs এ গড়ে প্রায় ৩.৬-৪.০% হলেও, বাংলাদেশ এই শ্রেণিতে থেকেও নিচে রয়েছে। বিশ্বের “শিক্ষার জন্য সুপারিশকৃত” GDP-এর অংশ প্রায় ৪-৬% যা অনেক আন্তর্জাতিক নীতি ও UNESCO, Education 2030 Framework এ বলা হয়েছে; এই মাত্রায় পৌঁছাতে বাংলাদেশকে আরো বড় অগ্রগতি করতে হবে।
বাজেটের কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে এই পরিসংখানে দেখা যায়, নেপালে ২০২০-২০২১ সালে শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটের প্রায় ১১-১২.৮২% অংশ দেওয়া হয়েছে; যা বাংলাদেশ-পাকিস্তান শোধিত সীমারেখার উপরে বা কাছাকাছি। পাকিস্তানে শিক্ষার জন্য সরকারি ব্যয়ের অংশ তুলনামূলকভাবে কম; ২০২৩-এ প্রায় ৮.৩৪%। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী বাজেটের প্রায় ১২% শিক্ষায় দেওয়া হচ্ছে; যদিও নির্দিষ্ট রিপোর্টে ব্যয় কতটা বাস্তবে হয়েছে তার বিস্তারিত ডেটা পাওয়া কঠিন। তবে বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া অর্থ সব সময় পুরোপুরি ব্যবহার হয় না; বাস্তব ব্যয় ও বরাদ্দের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।
অর্থনৈতিক সমস্যা ও বাধার কারণে তৈরি হওয়া সংকট
শিক্ষক সংকট ও নিম্ন বেতন: অপর্যাপ্ত বাজেটের কারণে স্কু ল ও কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরাও অনেক সময় নিম্ন বেতনে কাজ করেন, ফলে এই পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে।
অবকাঠামোগত দুর্বলতা: অনেক গ্রামীণ বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই, ফলে একাধিক শ্রেণি একসাথে পড়ানো হয়। এতে শিক্ষার্থীর শিখন-ফলাফল দুর্বল হয়।
গবেষণা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় সীমাবদ্ধতা: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নেই। উন্নত ল্যাব, লাইব্রেরি বা আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।
ড্রপআউট ও শিশু শ্রম: দরিদ্র পরিবারগুলো সন্তানের শিক্ষার খরচ বহন করতে না পেরে অনেক সময় তাদের পড়াশোনা বন্ধ করে কাজে পাঠায়। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ড্রপআউট হার বাড়ে।
কারিগরি ও উচ্চশিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার: কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও তহবিল স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ ধারার স্কু ল-কলেজে ভর্তি হয়। এতে কর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জন ব্যাহত হয়।
দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব
মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা: দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি না হওয়ায় দেশ বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যায়।
শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস: নিম্নমানের শিক্ষক ও অবকাঠামোর কারণে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে না।
সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি: ধনী ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষাগত সুযোগে পার্থক্য তৈরি হয়।
জাতীয় উন্নয়নে ধীরগতি: শিক্ষা ও অর্থনীতির আন্তঃসম্পর্কের কারণে সীমিত বিনিয়োগ জাতীয় উৎপাদনশীলতাকে সীমাবদ্ধ করে।
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অর্থনৈতিক বাধা একটি মৌলিক প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষাখাতকে শুধু ব্যয় নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারকে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো, শিক্ষাঋণ ও বৃত্তি কর্মসূচি জোরদার করা, এবং বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কাজে লাগাতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG 4) অর্জনের জন্য শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন অপরিহার্য।
৪) সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
সামাজিক প্রেক্ষাপট
দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য: বাংলাদেশে অনেক পরিবার শিশুদের পড়াশোনার খরচ বহন করতে পারে না, ফলে ড্রপআউট হার বেশি। দরিদ্র পরিবারগুলো শিশু শ্রমে বাধ্য করে।
গ্রাম-শহর বৈষম্য: শহরে তুলনামূলক ভালো মানের স্কু ল শিক্ষক ও অবকাঠামো থাকলেও গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে এ সুবিধা কম। এতে শিক্ষায় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।
লিঙ্গ বৈষম্য: মেয়েদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে অগ্রগতি হলেও এখনও অনেক এলাকায় সামাজিক কুসংস্কার, অল্প বয়সে বিয়ে ও নিরাপত্তাহীনতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
রাজনৈতিক প্রভাব: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্ররাজনীতি ও দলীয়করণ শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। পাঠ্যপুস্তকেও রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি (ব্রিটিশ আমল): ব্রিটিশ শাসনামলে (১৭৫৭–১৯৪৭) শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মূলত প্রশাসনিক কর্মচারী তৈরি করা, সৃজনশীল বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিকাশ নয় (Rahman, 2003)। ফলে শিক্ষা ছিল সীমিত ও নগরকেন্দ্রিক, যা সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে।
পাকিস্তান আমলের ভাষাকেন্দ্রিক সমস্যা (১৯৪৭–১৯৭১): পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে শিক্ষায় উর্দু-কেন্দ্রিক নীতি চালু করা হয়। এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) জন্ম নেয়। শিক্ষাখাত রাজনৈতিক বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হয়।
স্বাধীনতার পর পুনর্গঠন সংকট: মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অবকাঠামো ধ্বংস, দারিদ্র্য ও প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। কুদরত-এ-খুদা কমিশন (১৯৭৪) একটি আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর প্রস্তাব দিলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি।
শিক্ষাখাতের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তনে করনীয়
শিক্ষাখাতের সামগ্রিক উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্বাচনে জয়ের জন্য কিছু কাজ করলে হবে না। এজন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী, সমন্বিত উদ্যোগ এবং কাজ প্রয়োজন। উপরোক্ত বাস্তবতা ও সমস্যার আলোকে বিভিন্ন সেক্টরে অনেক কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে যা নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়-
১। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বোচ্চ ফল বের করা এবং শিক্ষিত, কর্মমূখি, উদ্যোগি, এবং কর্মঠ যুবশ্রেনী তৈরি করা।
২। কারিগরি শিক্ষাঃ কারিগরি শিক্ষার ব্যপক প্রসার এবং এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৩। উচ্চশিক্ষাঃ দেশের প্রয়োজনীয় এবং লভ্য কর্মসংস্থানের আলোকে উচ্চশিক্ষার আসন বন্টন এবং উচ্চশিক্ষিতরা যেন তাদের ডিগ্রী অনুযায়ী স্ব স্ব কাজে প্রবেশ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
৪। গবেষণা এবং উদ্ভাবনঃ বাছাইকৃত ভাগে গবেষণা এবং উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান করা এবং মৌলিক এবং ব্যবহারিক আবিস্কারে অনেক বেশী জোর দেয়া। উদ্ভাবন এবং আবিস্কারের জন্য উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মানী প্রদান।
৫। রাজনৈতিক সংস্কৃতিঃ প্রচলিত ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে।
About the Author:
মহব্বত আলী, পি.এইচ.ডি. বেলব্রুক ল্যাব, ম্যাডিসন, উইসকন্সিন -এ সিনিয়র সাইন্টিস্ট (।।), আর এন্ড ডি তে কর্মরত আছেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামজিক, ও রাজনৈতিক শিক্ষা ও গবেষণার সাথে জড়িত। He can be reached at mahbbatali10@gmail.com
Disclaimer: The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect The Insighta’s editorial stance. However, any errors in the stated facts or figures may be corrected if supported by verifiable evidence.